শিবাজীর শাসনব্যবস্থা ( Shivaji’s regime )
বিজেতা, সংগঠক, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, কুশলী যুদ্ধনায়ক এবং একজন সুদক্ষ শাসক হিসেবে শিবাজী ও শিবাজীর শাসনব্যবস্থা ( Shivaji’s regime ) স্মরণীয়।
এক সাধারণ জায়গীরদারের পুত্র হয়ে নিজের প্রতিভায় এক স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
বিধর্মী রাজশক্তি মুঘল সম্রাট ও বিজাপুরের সুলতানকে শিবাজী সুকৌশলে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর চরিত্র চতুরতায় পূর্ণ।
এই চতুরতা শিবাজীর চরিত্রকে ম্লান করেনি,বরং আলাদা মহিমা দিয়েছে।
শিবাজীর গেরিলা যুদ্ধনীতির জন্য কাফী খাঁ শিবাজীকে ‘শয়তানের চর’ ও ‘পর্বতের মূষিক’ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এতদসত্বেও শিবাজী ( Shivaji ) একজন সুদক্ষ শাসক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
শিবাজীর শাসন ব্যবস্থা সেইসময়ের ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। যদিও মালিক অম্বরের সংস্কার ও মুঘল শাসন ব্যবস্থায় তাঁর শাসন ব্যবস্থা পুষ্ট।
তবু তিনি নিজের প্রতিভায় মালিক অম্বর ও মুঘল শাসন ব্যবস্থার উপাদানগুলোকে মারাঠাদের উপযোগী করেছেন।
তাঁর শাসন ব্যবস্থা জনকল্যাণকামী দিকটিকেই তুলে ধরে। এইরূপ শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলি জানতে পোস্টটি অবশ্যই পড়তে হবে।
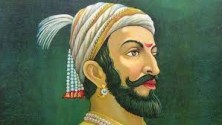
অষ্টপ্রধান মন্ত্রিপরিষদ ( Shivaji’s regime )
শিবাজী যে অঞ্চলগুলি অধিকার করেছিলেন সেগুলি দুধরণের। স্বরাজ্য ও মালাকাগিরি।
সরাসরি শিবাজীর শাসনাধীন ছিল স্বরাজ্য এলাকাগুলি।
এবং বশ্যতা ও কর প্রদানের শর্তে স্ব-শাসন ভোগ করতো মালাকাগিরি নামক এলাকাগুলি। কিন্তু শিবাজীর শাসন বেশি বলবৎ ছিল স্বরাজ্য এলাকাতেই।
মুঘল সম্রাটদের মতো শিবাজী স্বৈরতান্ত্রিক হলেও, প্রজাদের কল্যাণ করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। শাসনের সর্বোচ্চ পদে থাকতেন রাজা নিজেই।
রাজাকে শাসনকার্যে পরামর্শ দানের জন্য দরকার পড়তো কিছু লোকেদের।
সেই কারণে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে শিবাজীর রাজ্য অভিষেকের সময় অষ্টপ্রধান বা আটজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয়েছিল শিবাজীর মন্ত্রীপরিষদ।
এই অষ্টপ্রধানদের উপাধিগুলি প্রথমে ফারসি নামে হলেও পরে সংস্কৃতে বদলানো হয়েছিল।
পেশোয়া, অমাত্য, ওয়াকে-নভিস, সেনাপতি, পন্ডিতরাও, ন্যায়াধীশ, সুমন্ত বা দবীর, স্বর্ণবীশ বা সচিব এরাই হলেন অষ্টপ্রধান। এই অষ্টপ্রধানদের কাজগুলি ছিল,
পেশোয়া – পেশোয়া ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পেশোয়া গোটা শাসন ব্যবস্থার তদারকি করতেন।
অমাত্য – অমাত্য ছিলেন রাজস্ব বা অর্থমন্ত্রী। রাজস্ব সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বে থাকতেন তিনি।
ওয়াকে-নভিস – রাজার প্রতিদিনের কার্যকলাপ এবং রাজদরবারের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ লিখতেন।
সেনাপতি – ইনি সামরিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন।
পন্ডিতরাও – পন্ডিতরাও ছিলেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী। ধর্ম ও জাতপাত সংক্রান্ত বিবাদের বিচার করতেন। সেইসাথে ধর্মভ্রষ্টদের শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের হুকুম দান করতেন।
ন্যায়াধীশ – ন্যায়াধীশ ছিলেন প্রধান বিচারপতি। সমস্ত বিবাদের বিচারের ভার এনার হাতেই ন্যস্ত থাকতো।
সুমন্ত বা দবীর – বিদেশ দপ্তর দেখা ছিল এর কাজ। অর্থাৎ রাজ্যে বিদেশী দূতের আগমন ঘটলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো এবং তাঁর দেখভাল করাই ছিল দবীরের কাজ।
সচিব – সরকারি চিঠিপত্রের লেখক হিসেবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। কোনো ফরমান বা কোনো রাজপত্রের বিবরণ তাঁকে লিখতে হোতো।
বর্তমান ভারতের মন্ত্রীসভার মতো পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীরা দায়বদ্ধ ছিল না।
পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্বেও অন্যান্য মন্ত্রীরা একমাত্র শিবাজীর কাছেই দায়বদ্ধ থাকতেন।
কোনো মন্ত্রীদেরই নিজেদের অধীনে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা ছিল না। এই কর্মচারীও নিয়োগ করতেন ছত্রপতি শিবাজী স্বয়ং।
এর কারণ ছিল যাতে মন্ত্রীরা তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটাতে না পারে। এই আটজন মন্ত্রী ছাড়াও চিটনিস, সুবনীস, ফরনিশ, পটনিস, মজুমদার প্রমূখ অধস্তন কর্মচারীদের নামও পাওয়া যায়।
আরও পড়ুন : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাদেশিক শাসন
শিবাজীর রাজ্য কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশ একজন শাসনকর্তার অধীনে শাসিত হোতো।
এই শাসনকর্তাদের নিয়োগ করতেন রাজা শিবাজী নিজেই। প্রান্তগুলি বিভক্ত ছিল পরগনা বা তরফে।
তরফের শাসনকর্তাকে বলা হোতো হাবিলদার। অন্যদিকে প্রান্তের শাসক পরিচিত ছিলেন মামলাতদার নামে।
শিবাজীর রাজ্যের ক্ষুদ্রতম একক ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসন ব্যবস্থা পরিদর্শন করতেন দেশমুখ ও দেশপান্ডে নামক কর্মচারীরা।
এছাড়াও গ্রাম শাসনে পাতিল নামক কর্মচারীর ভূমিকার কথাও জানা যায়। পাতিল গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।
শিবাজীর রাজস্ব ব্যবস্থা
শিবাজী রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থায় মালিক অম্বরের নীতি অনুসরণ করেছিলেন।
রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে উৎপন্ন ফসলের প্রথমে ত্রিশ ভাগ ও পরে চল্লিশ ভাগ রাজস্ব ধার্য করা হয়। কৃষকরা এই রাজস্ব শস্য অথবা নগদের বিনিময়ে প্রদান করতো।
কৃষিকার্যকে উৎসাহ দিতে সরকার থেকে গরু-মহিষ ক্রয় করার ঋণ পর্যন্ত কৃষকদের দেওয়া হোতো।
মহারাষ্ট্র পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত ছিল। এখানকার রুক্ষ জমিতে শস্য কম ফলায় রাজকোষে কৃষি থেকে কম অর্থ আসতো।
তার ওপর শিবাজীর সামরিক বাহিনীর খরচ জোগাতে দরকার পড়তো প্রচূর অর্থের। দরকার ছিল মজবুত আর্থিক ব্যবস্থার।
১) চৌথ কর
সেইকারণে মারাঠাদের প্রতিবেশী অঞ্চল বিজাপুর, মুঘল অধিকৃত কয়েকটি জেলা থেকে শিবাজী চৌথ ও সরদেশমুখী কর আদায় করতেন।
চৌথ ছিল রাজস্বের এক চতুর্থাংশ কর। যে অঞ্চলগুলি চৌথ কর দিতে অস্বীকার করতো তারা মারাঠা ঘোড় সওয়ার সৈন্যদের দ্বারা লুন্ঠিত হোতো।
এই করটি সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচতে, অনেকটা নিষ্কৃতি কর ছিল।
২) সরদেশমুখী কর
অন্যদিকে সরদেশমুখী কথাটি এসেছে সরদেশমুখ থেকে।
সরদেশমুখ-র অর্থ প্রধান। শিবাজী ছিলেন মারাঠা রাজ্যের প্রধান।
তাই শিবাজীর অনুগত অঞ্চলগুলি থেকে এক দশমাংশ সরদেশমুখী কর শিবাজী আদায় করতেন।
তবে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে, শিবাজীর এইরূপ কর আদায় মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। এরফলে শিবাজীর সুনাম নষ্ট হয় এবং সাধারণ মানুষের কাছে মারাঠাদের পরিচয় হয় দস্যু হিসেবে।
সামরিক শাসন
মারাঠা সামরিক সংগঠন ব্যবস্থায় শিবাজীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মারাঠা সেনাদল গঠিত ছিল অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে। এই সৈন্যরা প্রথমদিকে কৃষিজীবী ছিল।
কৃষিকাজ যখন বন্ধ থাকতো কেবলমাত্র তখনই তাঁরা মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতো। শিবাজী এই ব্যবস্থার বিলুপ্ত করলেন।
বেতনের মাধ্যমে এক স্থায়ী সেনাদল গঠন করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শিবাজী নিজেই সেনা পরিচালনা করতেন।
মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনীকে বর্গী ও শিলাদার নামে দুটি শ্রেণীতে তিনি ভাগ করে দেন।
যে অশ্বারোহী সৈন্যরা রাজসরকার থেকে অস্ত্র, বর্ম, ঘোড়া পেতো তাঁদের নাম ছিল পাগা। এই পাগা সৈন্যদের ফারসি ভাষায় বলা হোতো বারগির। এই বারগির শব্দটি থেকেই পরে বর্গী কথাটি এসেছিল।
আর যে অশ্বারোহী সৈন্যরা নিজেদের অর্থে অস্ত্র, বর্ম, ঘোড়া কিনে যুদ্ধে যোগদান করতো তাঁরা পরিচিত ছিল শিলাদার নামে।
এঁরা ছিল মূলত ভাড়াটে সৈন্য। এছাড়াও ছিল হাবিলদার, জুমলাদার, হাজারি, সরনোবোত ইত্যাদি সেনা পরিচালকেরা।
শিবাজী তাঁর সামরিক ব্যবস্থায় বেশ কিছু দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের মতো পর্বতঘেরা জায়গায় দুর্গগুলি গেরিলা যুদ্ধের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।
এই গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধই ছিল শিবাজীর অন্যতম সামরিক কৌশল।
শিবাজীর নৌবহর
শিবাজী একটি উৎকৃষ্ট নৌবহর গঠন করেন। শিবাজীর নৌবাহিনীতে প্রায় চারশো নৌকো ও যুদ্ধজাহাজ ছিল।
এই নৌবাহিনীতে সৈন্য হিসেবে যোগ দিয়েছিল বোম্বাই উপকূলের অধস্তন জাতির লোকজনেরা।
নৌ-সেনাপতি আঙ্গিয়ারের অধীনে থাকা নৌবহরগুলি ইংরেজ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ নৌবাহিনীকে যথেষ্ট সমস্যায় ফেলেছিল।
এছাড়াও শিবাজীর ছিল বিশেষ হাতি ও উট বাহিনী। তবে শিবাজী তাঁর সৈন্যদলে শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেছিলেন।
জানা যায় যে, যদি কোনো স্ত্রীলোক মারাঠাদের সামরিক শিবিরে প্রবেশ করতো তাহলে তাঁর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। তাছাড়াও গবাদি পশুর হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।
শাসনব্যবস্থার মূল্যায়ণ
যদি শিবাজীর শাসনব্যবস্থার মূল্যায়ণ করতে হয় তাহলে বলা যায় এই শাসনব্যবস্থা ত্রূটিমুক্ত ছিল না।
প্রথমত, অষ্টপ্রধানরা স্বাধীন ক্ষমতা পাননি। শিবাজীর হাতে পুরো প্রশাসনের রাশ থাকায় শিবাজীর মৃত্যুর পর এই শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল।
দ্বিতীয়ত, জায়গীর প্রথা ও জমিদারী প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ তিনি ঘটাতে পারেননি।
তৃতীয়ত, গায়ের জোরে চৌথ ও সরদেশমুখী কর আদায় মারাঠাদের দস্যুতে পরিণত করে। কারণ এই কর আদায়ের ফলে শিবাজীর সুনাম নষ্ট হয়।
চতুর্থত, শিবাজী তাঁর বিচার ব্যবস্থাকে তেমন একটা সংগঠিত রূপ দিতে পারেননি।
পঞ্চমত, ভূমিরাজস্বের হার এতটাই বেশি ছিল যে, কৃষকদের দুর্দশা এইসময় বৃদ্ধি পায়। তার উপর রাজস্ব আদরকারীগণ ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠূর ও অত্যাচারী।
কিন্তু পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেও শিবাজী গড়ে তুলেছিলেন এক ধর্মরাজ্য।
আর তার শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল হিন্দু ধর্মের উপর ভিত্তি করে। তবুও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ছিল সমুজ্জ্বল।
তাই ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছেন, ”He organised an administration which was in many respects more efficient than that of the Mughals”.
আরও পড়ুন : ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরি
আশা করবো শিবাজীর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এই পোস্টটি পড়ে অনেক তথ্য জানতে পেরেছো। যদি পোস্টটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে তোমার মতামত জানিও। আর অবশ্যই পোস্টটি অন্যদের সাথে শেয়ার কোরো। তোমার মূল্যবান মতামত আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাতে সাহায্য করে। ভালো থেকো বন্ধু…..

